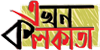BREAKING NEWS
🔴
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ, নিউ টাউন থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত, উদ্ধার নগদ টাকা এবং সোনার মুদ্রা
🔴
ইছাপুরে গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে বচসা-হাতাহাতি, হাসপাতালে নিয়ে গেলে যুবককে মৃত্যু, পিটিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার এক
🔴
বালি পাচার মামলায় আসানসোল-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ইডির অভিযান, কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের অফিসে চলছে তল্লাশি
🔴
শিবির বদলে পাওয়া গেল ‘ক্লিনচিট’! কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস খুনের ঘটনার ‘অভিযুক্ত’ নির্মল ঘোষকে দলে নিল তৃণমূল, বিতর্ক শুরু
🔴
ভবানীপুরে বস্তি ভেঙে পরিকল্পিত ভাবে ‘বহিরাগত’ প্রবেশ করানো হচ্ছে! বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান থেকে অভিযোগ বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতার
🔴
এলজেপি’র বিরুদ্ধে চারটি আসনে প্রার্থী দিল জেডিইউ, বিজেপির পরে প্রথম দফায় ৫৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল নীতীশের দল, রাজনৈতিক জল্পনা শুরু
🔴
ফের মেট্রো বিভ্রাট! এমজি রোড স্টেশনে লাইনে সমস্যা, বেশ কিছু ক্ষণ ভাঙা পথে চলল ট্রেন
🔴
সংগঠনে মনোনিবেশ, বিহার নির্বাচনের প্রার্থী হচ্ছেন না প্রশান্ত কিশোর, বিহার থেকে বিদায় নেবে এনডিএ, দাবি পিকের
🔴
রাজস্থানের জয়সলমেরে চলন্ত বাসে আচমকা আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু কমপক্ষে ১৯ জনের
🔴
ফের আক্রান্ত পুলিশ! ছিঁড়ল পুলিশকর্মীর উর্দি, শিশুমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত এগরা হাসপাতাল চত্বর
🔴
দুর্গাপুরকান্ডে গ্রেফতার নির্যাতিতার সহপাঠী, ধর্ষক এক জনই, অনুমান পুলিশের, খতিয়ে দেখা হচ্ছে বাকি ধৃতদের ভূমিকাও
🔴
নাগরাকাটায় বিজেপির খগেন এবং শঙ্করকে মারধরের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল হাই কোর্ট, পুলিকে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতির
🔴
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই নকল করে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ, গ্রেফতার ঘাটাল পুরসভার দলীয় কাউন্সিলর
🔴
লালুর বাছাই করা প্রার্থী পছন্দ নয় পুত্র তেজস্বীর! দলীয় প্রতীক পাওয়ার পরেও ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ, ভোটের আগে সরগরম বিহারের রাজনীতি
🔴
‘ভুটানও ক্ষতিপূরণ দিক’ নাগরাকাটার দুর্যোগকবলিত এলাকায় গিয়ে দাবি মমতার, কথা বললেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে
🔴
‘ছ’বছর ধরে কী করছিল সিবিআই?’ রাজীব কুমারের মামলায় ‘বিস্ময়’ প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের, আগামী শুক্রবার ফের শুনবেন দেশের প্রধান বিচারপতি
🔴
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নাম করে প্রতারণা, ‘অজানা’ লিঙ্কে ক্লিক করতেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব! পুলিশের জালে ছ’জন
🔴
বকাবকি করেছিলেন মৌলানা! প্রতিশোধ নিতে স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে মাথায় হাতুড়ি এবং ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন, বাগপত-কান্ডে আটক দুই মাদ্রাসার ছাত্র
🔴
এসএসসির শিক্ষাকর্মী নিয়োগে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট, নিয়োগের ‘সময়সীমা’ বেঁধে দেওয়ার আর্জি খারিজ শীর্ষ আদালতে
🔴
গণধর্ষণ-কান্ডের প্রতিবাদ দুর্গাপুরে, ধর্ণামঞ্চ খুলতে এলে পুলিশের সঙ্গে বচসা বিজেপি কর্মীদের, নির্যাতিতার বাবাকে নিয়ে পৌঁছোলেন শুভেন্দু
🔴
দুর্গাপুরে গণধর্ষণ-কান্ডে অবশেষে গ্রেফতার পঞ্চম অভিযুক্ত, সব মিলিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ, এখনও আটক তরুণীর সহপাঠী
🔴
দুর্গাপুরের ডাক্তারি ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার পুরসভার অস্থায়ী কর্মী! ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল চারজন
🔴
উত্তরপ্রদেশের বাগপতের মসজিদের কক্ষে মৌলানার স্ত্রী এবং দুই মেয়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, আটক দুই মাদ্রাসার ছাত্র, উদ্ধার অস্ত্র
🔴
ট্রেন ঢুকতেই বর্ধমান স্টেশনে হুড়োহুড়ি, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পদপিষ্ট হয়ে জখম অন্তত সাতজন, ভর্তি করা হল বর্ধমান মেডিকেলে
🔴
‘রাতে মেয়েদের বাইরে বেরোতে দেওয়া উচিত নয়’, দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কান্ড নিয়ে মন্তব্য মমতার, কটাক্ষ বিজেপির
🔴
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ, নিউ টাউন থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত, উদ্ধার নগদ টাকা এবং সোনার মুদ্রা
🔴
ইছাপুরে গাড়ি পার্কিং করা নিয়ে বচসা-হাতাহাতি, হাসপাতালে নিয়ে গেলে যুবককে মৃত্যু, পিটিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার এক
🔴
বালি পাচার মামলায় আসানসোল-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ইডির অভিযান, কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের অফিসে চলছে তল্লাশি
🔴
শিবির বদলে পাওয়া গেল ‘ক্লিনচিট’! কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস খুনের ঘটনার ‘অভিযুক্ত’ নির্মল ঘোষকে দলে নিল তৃণমূল, বিতর্ক শুরু
🔴
ভবানীপুরে বস্তি ভেঙে পরিকল্পিত ভাবে ‘বহিরাগত’ প্রবেশ করানো হচ্ছে! বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান থেকে অভিযোগ বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতার
🔴
এলজেপি’র বিরুদ্ধে চারটি আসনে প্রার্থী দিল জেডিইউ, বিজেপির পরে প্রথম দফায় ৫৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল নীতীশের দল, রাজনৈতিক জল্পনা শুরু
🔴
ফের মেট্রো বিভ্রাট! এমজি রোড স্টেশনে লাইনে সমস্যা, বেশ কিছু ক্ষণ ভাঙা পথে চলল ট্রেন
🔴
সংগঠনে মনোনিবেশ, বিহার নির্বাচনের প্রার্থী হচ্ছেন না প্রশান্ত কিশোর, বিহার থেকে বিদায় নেবে এনডিএ, দাবি পিকের
🔴
রাজস্থানের জয়সলমেরে চলন্ত বাসে আচমকা আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু কমপক্ষে ১৯ জনের
🔴
ফের আক্রান্ত পুলিশ! ছিঁড়ল পুলিশকর্মীর উর্দি, শিশুমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত এগরা হাসপাতাল চত্বর
🔴
দুর্গাপুরকান্ডে গ্রেফতার নির্যাতিতার সহপাঠী, ধর্ষক এক জনই, অনুমান পুলিশের, খতিয়ে দেখা হচ্ছে বাকি ধৃতদের ভূমিকাও
🔴
নাগরাকাটায় বিজেপির খগেন এবং শঙ্করকে মারধরের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল হাই কোর্ট, পুলিকে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতির
🔴
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই নকল করে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণার অভিযোগ, গ্রেফতার ঘাটাল পুরসভার দলীয় কাউন্সিলর
🔴
লালুর বাছাই করা প্রার্থী পছন্দ নয় পুত্র তেজস্বীর! দলীয় প্রতীক পাওয়ার পরেও ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ, ভোটের আগে সরগরম বিহারের রাজনীতি
🔴
‘ভুটানও ক্ষতিপূরণ দিক’ নাগরাকাটার দুর্যোগকবলিত এলাকায় গিয়ে দাবি মমতার, কথা বললেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে
🔴
‘ছ’বছর ধরে কী করছিল সিবিআই?’ রাজীব কুমারের মামলায় ‘বিস্ময়’ প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের, আগামী শুক্রবার ফের শুনবেন দেশের প্রধান বিচারপতি
🔴
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নাম করে প্রতারণা, ‘অজানা’ লিঙ্কে ক্লিক করতেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব! পুলিশের জালে ছ’জন
🔴
বকাবকি করেছিলেন মৌলানা! প্রতিশোধ নিতে স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে মাথায় হাতুড়ি এবং ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন, বাগপত-কান্ডে আটক দুই মাদ্রাসার ছাত্র
🔴
এসএসসির শিক্ষাকর্মী নিয়োগে হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট, নিয়োগের ‘সময়সীমা’ বেঁধে দেওয়ার আর্জি খারিজ শীর্ষ আদালতে
🔴
গণধর্ষণ-কান্ডের প্রতিবাদ দুর্গাপুরে, ধর্ণামঞ্চ খুলতে এলে পুলিশের সঙ্গে বচসা বিজেপি কর্মীদের, নির্যাতিতার বাবাকে নিয়ে পৌঁছোলেন শুভেন্দু
🔴
দুর্গাপুরে গণধর্ষণ-কান্ডে অবশেষে গ্রেফতার পঞ্চম অভিযুক্ত, সব মিলিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ, এখনও আটক তরুণীর সহপাঠী
🔴
দুর্গাপুরের ডাক্তারি ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার পুরসভার অস্থায়ী কর্মী! ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল চারজন
🔴
উত্তরপ্রদেশের বাগপতের মসজিদের কক্ষে মৌলানার স্ত্রী এবং দুই মেয়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, আটক দুই মাদ্রাসার ছাত্র, উদ্ধার অস্ত্র
🔴
ট্রেন ঢুকতেই বর্ধমান স্টেশনে হুড়োহুড়ি, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পদপিষ্ট হয়ে জখম অন্তত সাতজন, ভর্তি করা হল বর্ধমান মেডিকেলে
🔴
‘রাতে মেয়েদের বাইরে বেরোতে দেওয়া উচিত নয়’, দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কান্ড নিয়ে মন্তব্য মমতার, কটাক্ষ বিজেপির